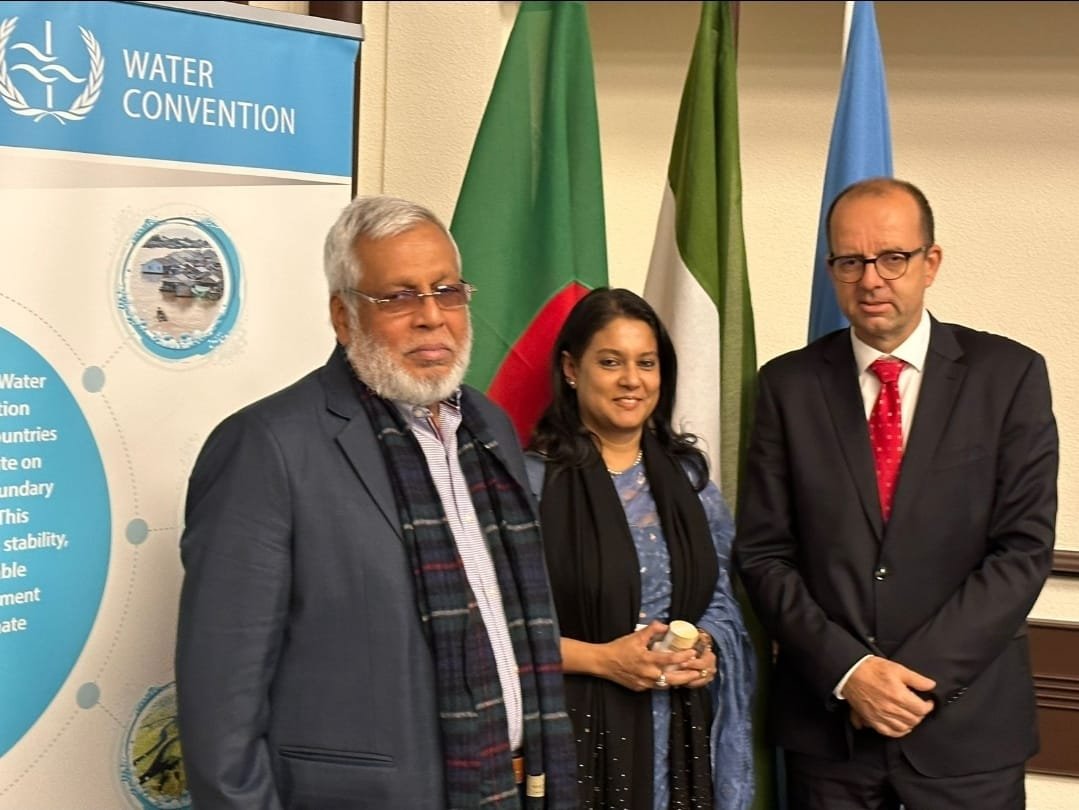ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ‘অস্থায়ী কারাগার’ ঘোষণা ও সেনা হেফাজত: আইন, প্রশ্ন ও জনতার উদ্বেগ
কেন্দ্রীয় পয়েন্ট: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেজেট নোটিশে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের একটি ভবনকে ‘অস্থায়ী কারাগার’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একই সময় সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে ১৫ জন (প্রধান সংবাদসূত্রের হিসাবে) সেনা কর্মকর্তা বর্তমানে তাদের হেফাজতে আছেন; এসব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ICT-র পক্ষ থেকে অভিযোগ ও গ্রেফতারের নির্দেশনার কথা বলা হচ্ছে।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ‘অস্থায়ী কারাগার’ ঘোষণা ও সেনা হেফাজত: আইন, প্রশ্ন ও জনতার উদ্বেগ
ঢাকা, ১৩ অক্টোবর ২০২৫ — দেশের রাজনৈতিক-আইনি অঙ্গনে এক নতুন আঘাত বলেই বিবেচিত হচ্ছে—বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিশে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের একটি ভবনকে অস্থায়ী কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনী স্বীকার করেছে যে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে তারা হেফাজতে নিয়েছে। সূত্রগুলো বলছে আদালত-উঠানো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) কয়েকটি গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট জারি হওয়ার পরে ঘটনাগুলো ঘটেছে।
কেন্দ্রীয় পয়েন্ট: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেজেট নোটিশে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের একটি ভবনকে ‘অস্থায়ী কারাগার’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একই সময় সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে ১৫ জন (প্রধান সংবাদসূত্রের হিসাবে) সেনা কর্মকর্তা বর্তমানে তাদের হেফাজতে আছেন; এসব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ICT-র পক্ষ থেকে অভিযোগ ও গ্রেফতারের নির্দেশনার কথা বলা হচ্ছে।
সরকারি নোটিফিকেশনে ওই ভবনকে অস্থায়ী কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে—যা প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতায় আনা হয়। আমলা হিসেবে মন্ত্রণালয় গেজেট নোটিশ জারি করার মাধ্যমে জেলায় ব্যবহারের জন্য কোনো স্থাপনা ঘোষণা করে থাকতে পারে; সাংবাদিক রিপোর্টগুলোও এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।
তবে আইনগত প্রক্রিয়ার মূল কন্ডিশন কিন্তু আলাদা: যেসব ব্যক্তিকে ‘গ্রেফতার’ বলা হয়, গ্রেফতারের পরে তাদের আইন অনুযায়ী আদালতে (বা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে) দ্রুত উপস্থাপন করতে হয়—বাংলাদেশের প্রসঙ্গেও গ্রেফতারের পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত ২৪ ঘণ্টা) আদালতে দেখানোর বিধান প্রসঙ্গে স্বীকৃত ব্যাখ্যা রয়েছে; আইনি বিশ্লেষকরা বলছেন গ্রেফতারের স্ট্যাটাস স্পষ্ট না হলে ওই বিধান প্রযোজ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
সেনাবাহিনীর কেসে ভিন্ন দিক: সেনা সদস্যরা যদি ‘Army Act’ বা সামরিক বিধির আওতাভুক্ত হন, তাহলে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজ নিয়মে তাঁদের হেফাজতে রাখতে পারে—তবে তা হলেও মৌলিক সংবিধানগত অধিকার (নির্যাতন-নিষেধ, বিচারিক প্রাপ্যতা, আইনজীবীর সাথে দেখা ইত্যাদি) রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সংবাদ-সূত্র অনুযায়ী সেনাবাহিনী নিজের ভেতরে কিছু কর্মকর্তাকে ‘শান্তভাবে’ হেফাজতে নিয়েছে বলে জানিয়েছে; কিন্তু একই সঙ্গে ICT-এর প্রসঙ্গ, সাধারণ আদালত-প্রসস্তি ও পুলিশি কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও জটিলতা তৈরি করছে।
সংক্ষেপে: প্রশাসনিকভাবে ‘অস্থায়ী কারাগার’ ঘোষণার ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু যদি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বলা হয় বা আদালতের নির্দেশের বাইরে দীর্ঘসময় রাখা হয়—তাহলে সেটি সংবিধান ও দণ্ডবিধির (CrPC) নিয়মের আলোকে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। মামলার ধরনের (ICT-ওয়ারেন্ট, সামরিক-কেস) ওপরও ভিন্ন বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।
---
২) যদি সেনা কর্মকর্তাদের সেনা ভবনে রাখা যায়, তাহলে রাজনৈতিক নেতারা, পুলিশ বা সরকারি আমলাদের কেন তাদের অফিস/থানায় রাখা যাবে না?
এখানে মূল বিষয়টি হল আইনি ভেন্যু (venue) ও কর্তৃত্ব: সামরিক সদস্যদের ক্ষেত্রে সামরিক বিধি (Army Act) প্রযোজ্য হওয়ায় তাদেরকে সামরিক কাস্টডিতে রাখার ঐতিহ্যগত ও আইনগত সুযোগ থাকতে পারে। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতা, পুলিশকর্মী বা সরকারি আমলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত সিআরপি/সিভিল কোর্ট ও পুলিশের অধীনে থাকা বিধি প্রযোজ্য হয়—তাই তাদেরকে দলীয় অফিস, থানায় বা সচিবালয়ে রাখার প্রশ্নে আলাদা আইনি ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থাকে।
নীতিগত ন্যায্যতা (principle of equality): নাগরিকদের প্রশ্ন আছে—“একই কাজ, কেন একেক জায়গায়?”—এই প্রশ্নটি ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার কারণে যৌক্তিক। আইনি সমানতায় (‘equality before law’) এমন পার্থক্য হওয়া উচিত কি না—এটাই বড় প্রশ্ন, এবং এটি বিচারিক ও সাংবিধানিক পর্যায়ে চেক হওয়া দরকার। সরকারি ও সামরিক দু’পক্ষকে একই মানদণ্ডে স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে।
---
৩) বিচারিক প্রক্রিয়ার বদলে ‘ভবনে রাখা’–র সিদ্ধান্ত কে নিল?
যে অংশটি প্রশাসনিক: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেজেট নোটিশ জারি করে ভবনকে অস্থায়ী কারাগার ঘোষণা করেছে—অর্থাৎ ‘কোথায় কাউকে রাখা হবে’—এই সিদ্ধান্ত সাধারণ প্রশাসনিক একশনে আসে। একই সময়ে সেনাবাহিনী নিজ দায়িত্বে এবং নিজের কর্তৃত্বাধীন রিজিমে বলে তারা ওই কর্মকর্তাদের হেফাজতে নিয়েছে—এখানে সেনা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে বলে সংবাদে উল্লেখ আছে। তবে ‘গ্রেফতারের আইনি স্ট্যাটাস’–এর বিষয়ে কোর্ট/ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা আলাদা—আদালতই নির্ধারণ করবেন কার ওপর কি ধাঁচের রিমান্ড বা রক্ষণাবেক্ষণ আরোপ হবে।
---
৪) একই কাজের জন্য কেন দুই ধরনের ফল? (দুইভাবে ব্যবহৃত ভেন্যু ও ফলাফল কেন?)
সহজ ব্যাখ্যা: আইনের বিভাজন ও কর্তৃত্ব—সামরিক সদস্যের উপর সামরিক বিধি আর সাধারণ নাগরিকদের উপর সিভিল ক্রিমিনাল প্রসিডিউর পৃথক। ফলে প্র্যাকটিক্যালি সমান অভিযোগ থাকলেও ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ হতে পারে।
আরেকটি বাস্তব কারণ হল নিরাপত্তা ও তদন্তগত বিবেচনা—সংবেদনশীল মামলা হলে কর্তৃপক্ষ দ্রুত নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু এ সব হলে স্বচ্ছতা না থাকলে জনমনে সন্দেহ ও মানবাধিকার-উদ্বেগ বাড়ে—এ জন্য স্বচ্ছ তদারকি, আদালত-উপস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান জরুরি।
---
সেনাবাহিনী-প্রতিনিধি মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন যে ওই কর্মকর্তারা সেনা কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে এবং ICT-এর ওয়ারেন্টের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই সক্রিয় দায়িত্মান ছিলেন; এক বা দু’জনকে ‘AWOL’ বা অনুপস্থিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
জনগণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে—একাংশ জনগণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে দ্রুত একাউন্টেবিলিটি দাবি করছে, অন্যরা বলছে প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া দরকার এবং আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোও এই আবেগ-উদ্বেগ তুলে এনেছে।
1. স্বচ্ছ প্রকাশ: সরকার ও সেনাবাহিনী—দু’পক্ষই স্পষ্ট করে সরকারি নথি ও আইনি ব্যাখ্যা প্রকাশ করুন: কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, কারা তদন্ত করছেন, আদালতে কখন উপস্থাপন করা হবে।
2. বিচারিক তদারকি: যদি গ্রেফতারের স্ট্যাটাস প্রযোজ্য হয়, আইন অনুযায়ী দ্রুত আদালতে উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে—CrPC/আইনগত সময়সীমা মেনে চলা অপরিহার্য।
3. মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ: নিরপেক্ষ মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ও আইনজীবীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন; নির্যাতন-বিরোধী গ্যারান্টি থাকা
4. সমতার নীতি: একই ধরনের অভিযোগে ভিন্ন ভেন্যু বা ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইনগত ব্যাখ্যা ও কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন—না হলে দেশব্যাপী ভুল বার্তা যাবে।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একটি ভবনকে অস্থায়ী কারাগার ঘোষণা এবং সেনা কর্মকর্তাদের সেনা হেফাজতে রাখার খবর দেশের জন্য বড় আইনি-সামাজিক প্রশ্ন তোলে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত-নেওয়া ও সামরিক কাস্টডি-প্রয়োগ যখন ঘটে—সেই সঙ্গে দ্রুত বিচারিক তদারকি, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার-প্রটেকশন নিশ্চিত করা না হলে পাবলিক ট্রাস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—আইনগত স্ট্যাটাস স্পষ্ট করা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আদালতে দ্রুত উপস্থাপন, এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা—এগুলোই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত ও দেশের আইনি নীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে।